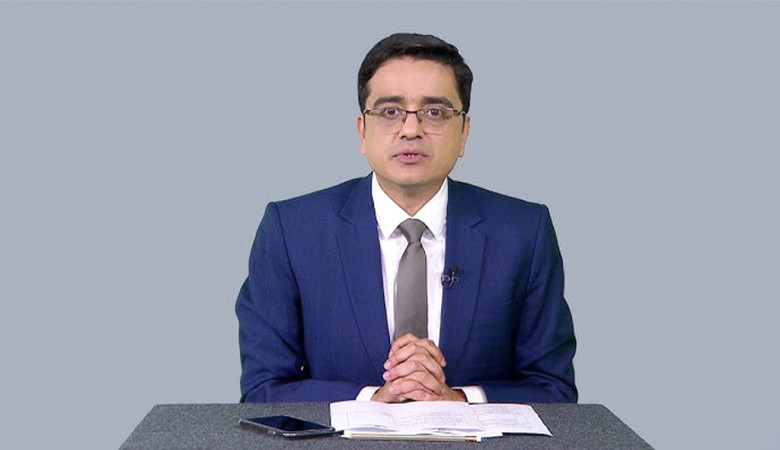খালেদ মুহিউদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত
এক পাশে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, অন্য পাশে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাঝখানে উপস্থাপক ও সাংবাদিক খালেদ মুহিউদ্দীন—ইউটিউবে কথিত একটি ‘টকশো’তে তিনজনকে এভাবেই দেখা যায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা কখনোই সুপরিচিত উপস্থাপক খালেদ মুহিউদ্দীনের টকশোতে (আলোচনা অনুষ্ঠান) যাননি; কিন্তু ইউটিউবে কারসাজি করে এমন টকশো তৈরি করা হয়েছে। এতে ব্যবহার করা হয়েছে খণ্ড খণ্ড ভিডিও চিত্র (ক্লিপ)। তা দেখে অনেক দর্শকের কাছে মনে হতে পারে, টকশোতে অতিথিরাই কথা বলছেন।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ক্যামেরার দিকে মুখ করে দুই নেত্রী অনলাইনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ‘ভার্চুয়াল টকশো’তে অংশ নিয়েছেন। সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীন শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানান, ২০২৪ সালের আগস্টে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে। কিছুক্ষণ যেতেই অনেক দর্শক বুঝবেন, ভিডিওটি ভুয়া। খালেদা জিয়ার নড়াচড়া স্বাভাবিক না। শেখ হাসিনার কণ্ঠস্বর তার মুখভঙ্গির সঙ্গে মিলছে না। খালেদার ভিডিও ফুটেজ বিকৃত বা টেনে লম্বা করা হয়েছে। উপস্থাপকের হাতের অঙ্গভঙ্গি বারবার একই রকম দেখা যাচ্ছিল। বিভিন্ন উৎস থেকে ক্লিপ কেটে জোড়া লাগিয়ে কথোপকথন তৈরি করে এ ভুয়া টকশো সাজানো হয়।
সুপরিচিত নবীন ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ, আলোচিত ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয় বিশ্লেষক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ‘ইনফ্লুয়েন্সার’দের নিয়ে এ ধরনের ভুয়া টকশো তৈরি করা হচ্ছে। এগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে খণ্ড খণ্ড ভিডিও চিত্র (ক্লিপ)। বানোয়াট এসব ভিডিও দেখে অনেকে বিশ্বাস করেন, টকশোর অতিথিরাই কথা বলছেন। অধিকাংশ ভিডিওতে মূল সাক্ষাৎকারগুলোকে প্রাসঙ্গিকতার বাইরে গিয়ে কাটাছেঁড়া করে এমনভাবে বানানো হয়, যা আদতে ঘটেনি। এতে বিভ্রান্ত হন দর্শকরা। উপস্থাপক, আলোচকের নামে ছড়িয়ে পড়ে ভুয়া মন্তব্য। তাদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। অনেক, পাঠক দর্শকের মধ্যে তাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মায়। কথিত মন্তব্যকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেটিজেনদের মধ্যে চলে নানামুখী আলোচনা।
বানোয়াট মন্তব্যকে এক রাজনৈতিক গোষ্ঠী পক্ষ-বিপক্ষ বিবেচনায় স্বাগত জানালেও অন্য গোষ্ঠী এর বিষোদগার করে; গালি দেয় আলোচক, উপস্থাপক, সঞ্চালককে। আক্রমণাত্মক ও অশোভন বাক্যে সমালোচনা করে। অথচ উপস্থাপক যে মাধ্যম, ইউটিউব চ্যানেলে ওই টকশো অনুষ্ঠান করেন, সেই ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে ভিডিও, বা কনটেন্টটি আপলোড হয়েছে কী না, আদৌ অনুষ্ঠানের ভিডিওটি সঠিক কী না, তা যাচাই-বাছাইয়ে অনেকের বেশ অনীহা রয়েছে।
এমনকি পেশাগত দিক বিবেচনায় যাদের সচেতন নাগরিক হিসেবে ধরা হয়, তাদের মধ্যে সাংবাদিক, কবি, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী, গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা রাজনৈতিক নেতাসহ বিভিন্ন পেশাজীবীকেও দেখা যায় সত্যতা যাচাই না করে ভুয়া ভিডিও, পত্রিকা ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের নামে বানানো ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করছেন, সেগুলোর বক্তব্য বিশ্বাস করছেন। এতে উপস্থাপক, আলোচক, বক্তা ও সংবাদমাধ্যমের নামে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। কখনো কখনো আলোচক ও প্রতিষ্ঠান মবের ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। এগুলোকে ঘিরে সমাজে প্রায় সময় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বলেও মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞ।
সুখবর ডটকমের নানাভাবে চালানো অনুসন্ধানে দেখা যায়, গত এক বছরের মধ্যে খালেদ মুহিউদ্দীনের টকশোর নামে ইউটিউবে ভুয়া ভিডিও বেশি প্রচারিত হয়েছে। এসব ভিডিওকে তার উপস্থাপনার টকশো বলে ভিউ বাণিজ্য করছে একশ্রেণির ইউটিউব চ্যানেল ও সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট। প্রবাসী সাংবাদিক খালেদ মুহিউদ্দীন ইউটিউবে ‘ঠিকানায় খালেদ মুহিউদ্দীন’ নামে একটি চ্যানেলে টকশো উপস্থাপনা করেন। তার ছবি, ফুটেজ ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্লিপ যুক্ত করে ভুয়া টকশো তৈরি করে প্রচার করা হচ্ছে। ইউটিউবে ‘খালেদ মুহিউদ্দীন টকশো’ লিখে খোঁজ করলে এমন কথিত চ্যানেলের লিংক পাওয়া যায়।
শুধু খালেদ মুহিউদ্দীন নন, অনৈতিকভাবে পরিচালনা করা ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে দেশের অন্যান্য উপস্থাপক ও রাজনৈতিক বক্তাদের বিভিন্ন বক্তব্যের ক্লিপ জুড়ে দিয়ে ভুয়া টকশোর ছড়াছড়ি। এগুলোতে ‘ব্যাকগ্রাউন্ড’ (নেপথ্যের দৃশ্য) বদলানো, ফুটেজ কাটাছেঁড়া বা জুম করা এবং মূল প্রসঙ্গ বিকৃত করা হয়েছে। অধিকাংশ ভিডিও ইউটিউব, টেলিভিশন শো, ফেসবুক লাইভ এবং অডিও রেকর্ডিং থেকে ক্লিপ জোড়া লাগিয়ে তৈরি। অনেক ক্ষেত্রে, মূল বক্তার ফুটেজে এমন ভয়েসওভার (কথা) জুড়ে দেওয়া হয়, যা ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে নেওয়া এবং যার সঙ্গে কথোপকথনের কোনো সম্পর্ক নেই; কিন্তু বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভুয়া টকশোতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ, সেখান থেকে টাকা আয়ের সুযোগের সম্ভাবনাও রয়েছে। ইউটিউবের নিজস্ব নীতিমালা ভঙ্গ করে বানানো এ ধরনের ভিডিও প্রচার করে ইউটিউব নিজেও লাভবান হচ্ছে। এ ধরনের ভুয়া টকশো অনেকে বিশ্বাস করেন, যার ফলে সমাজে বিভাজন তৈরি হয় এবং রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব পড়ে। যারা এসব 'কনটেন্ট' বানান, তারা জনপ্রিয়দের বেশি টার্গেট করেন। তাদের নামে ভিডিও, ফটোকার্ড বানানো হলে তুলনামূলক বেশি দর্শক পাওয়া যায়।
প্রসঙ্গত, সাংবাদিক খালেদ মুহিউদ্দীন টকশো উপস্থাপক হিসেবে দেশ-বিদেশের বাংলাভাষীদের কাছে তুমুল জনপ্রিয়। গত বছরের শেষ দিকে তিনি জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে ছেড়ে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ‘ঠিকানা’য় যোগ দেন। এখন তিনি ‘ঠিকানায় খালেদ মুহিউদ্দীন’ শিরোনামে টকশো উপস্থাপনা করেন। ডয়চে ভেলে’তে তার সঞ্চালনায় একটানা প্রায় চার বছর প্রচারিত টকশো ‘খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়’ বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। বলা হয়ে থাকে, জনপ্রিয়তার বিচারে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা'কে পেছনে ফেলে দেয় অনুষ্ঠানটি।
গুজবের মাঠে গত কয়েক ধরে ধরে নতুন অস্ত্র হয়ে ওঠেছে সংবাদমাধ্যমের নামে বানানো 'টকশো', 'ভিডিও' ও ‘ফটোকার্ড’। এতে সংবাদমাধ্যমগুলোর দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়ছে। একদিকে যেমন তৈরি হচ্ছে বিভ্রান্তি, অন্যদিকে এর পেছনে ব্যয় করতে হচ্ছে গণমাধ্যমগুলোর একটা ভালো পরিমাণ সময় ও জনবল। কারণ, প্রচারিত সংবাদকে বিকৃত করে যে সংবাদমাধ্যমের ব্যানারে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, এ গুজব শনাক্ত করতে গিয়ে সেই সংবাদমাধ্যমকে অতিরিক্ত তৎপর থাকতে হচ্ছে। তারা তৈরি করছে আরেকটি ফটোকার্ড, যেখানে তাদের নামে গুজববাজদের বানানো ভিডিও ও ফটোকার্ডের বিষয়ে পাঠক, দর্শককে সতর্ক করতে হয়। নকল ফটোকার্ড, ভিডিও যেমন অপতথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করছে, অন্যদিকে মূল সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রায় সময় করছে প্রশ্নবিদ্ধ।
সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ ও ভিউয়ারশিপ বাড়ানোর জন্য গণমাধ্যমগুলো ফটোকার্ড উদ্ভাবন করেছিল। ফটোকার্ড হচ্ছে মূলত একটি ছবি, যেখানে মূল খবরের শিরোনাম বা সারাংশ থাকে, এতে থাকে প্রাসঙ্গিক একটি ছবি। বিভিন্ন মিডিয়া তাদের লোগো দিয়ে নিজেদের জন্য প্রাসঙ্গিক একটা টেমপ্লেট বানিয়ে ফটোকার্ড শেয়ার করে থাকে। এতে সংবাদটি বেশি ভিউয়ারশিপ পায়। এ সহজলভ্য প্রযুক্তি বর্তমানে গুজব নির্মাতাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কারণ, ফটোকার্ড খুব সহজে সম্পাদনযোগ্য টেমপ্লেট।
অনেক গণমাধ্যম আগের মতো এখন আর সরাসরি খবরের লিংক ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে না। সামাজিক মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে ছবি, ভিডিওর জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব বেশি, তাই ফটোকার্ডের মাধ্যমে তারা খবর প্রকাশ করে। অনেকে এ পরিচয় ঠিক রেখে ছবিটি বিকৃত করে ভুয়া তথ্য জুড়ে দিচ্ছেন। আবার ভুয়া ফটোকার্ড ও ভিডিওকে ভিত্তি করে প্রায় সময় মূলধারার প্রচারমাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরির ঘটনাও ঘটছে।
যেমন, ঢাকার প্রথম সারির বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলের ওয়েবসাইটে ২০২৩ সালে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়, ডয়চে ভেলের টকশো ‘খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়’ তিন মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যা আদৌ সত্য ছিল না। ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া একটি ভিডিও থেকে তথ্য নিয়ে প্রতিবেদনটি সাজানো হয়। অবশ্য 'অনাকাঙ্ক্ষিত' এ ভুলের জন্য টিভি চ্যানেলটির পক্ষে পরে আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করা হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ৭ই জানুয়ারি। নির্বাচন ঘিরে খালেদ মুহিউদ্দীনকে জড়িয়ে একটি মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়ায় পরদিন ৮ই জানুয়ারি থেকে।
ওই মন্তব্যের সঙ্গে একটি ভিডিও জুড়ে দাবি করা হয়, খালেদ মুহিউদ্দীন সদ্য অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন নিয়ে বলেন, ‘৭০ উইকেটের বিনিময়ে অর্জন ৪০ শতাংশ, তার মধ্যে ৩৮ শতাংশ জাল, ২ শতাংশ কাস্ট। গত ১৫ বছরে এটাই তাদের (আওয়ামী লীগ) অর্জন...! সাংবাদিক হিসেবে আমি লজ্জিত।’ নেটিজেনদের ফেসবুকে প্রচারিত মন্তব্যটি খালেদ মুহিউদ্দীনের বক্তব্য হিসেবে বিশ্বাস করতে দেখা যায়। ঢাকা থেকে প্রচারিত একাধিক অনলাইন সংবাদমাধ্যমে তার এ 'বক্তব্য' নিয়ে প্রতিবেদন হয়৷ অথচ তিনি এমন কোনো মন্তব্য করেননি।
খবরটি শেয়ার করুন