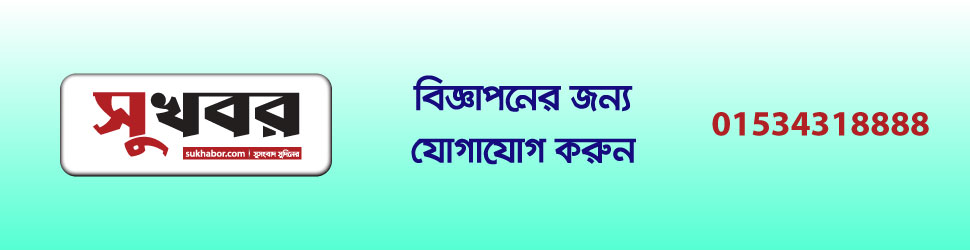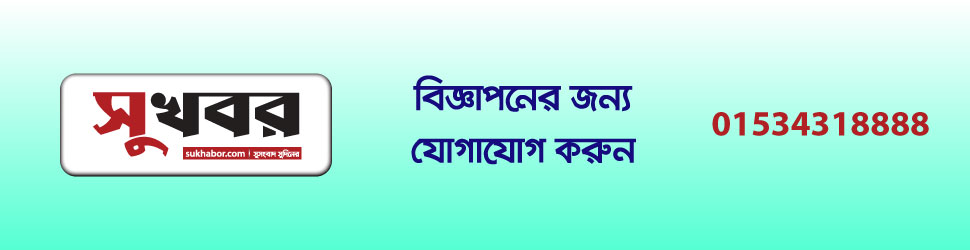ছবি: সংগৃহীত
সাঈদ মাহবুব
"হাজার বছর ধ’রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।"
জীবনানন্দ দাশ বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। তাকে রূপসী বাংলার কবিও বলা হয়। বুদ্ধদেব বসু তাকে ‘নির্জনতম কবি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া অনেকে তাকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি বলে মনে করেন। তার কবিতায় পরাবাস্তবের দেখা মিলে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে নজরুল ইসলামের প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী। জীবনানন্দ দাশ প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনাও প্রকাশ করেছেন। তিনি ২১টি উপন্যাস ও ১২৬টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন, যার একটিও তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।
বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অনপনেয়ভাবে বাংলা কবিতায় তার প্রভাব মুদ্রিত হয়। ‘বনলতা সেন’ কাব্যের কবিতাগুলোসহ পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ ‘মহাপৃথিবী’ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত। জীবনানন্দের জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবির মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো ১৯৫৭-তে প্রকাশিত ‘রূপসী বাংলা’ এবং ১৯৬১-তে প্রকাশিত ‘বেলা অবেলা কালবেলা’।
জীবনানন্দ দাশ ‘রূপসী বাংলা'র পাণ্ডুলিপি তৈরি করে থাকলেও জীবদ্দশায় এর প্রকাশের উদ্যোগ নেননি। তিনি গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম নির্ধারণ করেছিলেন ‘বাংলার ত্রস্ত নীলিমা’। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশকালে এর নামকরণ করা হয় ‘রূপসী বাংলা’। তার অগ্রন্থিত কবিতাবলি নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলো হলো: সুদর্শনা (১৯৭৩), আলো পৃথিবী (১৯৮১), মনোবিহঙ্গম, হে প্রেম, তোমারে ভেবে ভেবে (১৯৯৮), অপ্রকাশিত একান্ন (১৯৯৯) এবং আবছায়া (২০০৪) প্রভৃতি।
এ ছাড়া জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা, শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি। এরমধ্যে জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থ নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত (১৯৫৩) হয়। ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি ভারত সরকারের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করে।
জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয় অজস্র গল্প ও উপন্যাস। এগুলোর প্রথম সংকলন জীবনানন্দ দাশের গল্প (১৯৭২, সম্পাদনা: সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী)। বেশ কিছুকাল পর প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৯- সম্পাদনা: আবদুল মান্নান সৈয়দ)। তার প্রকাশিত ১৪টি উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মাল্যবান (১৯৭৩), সুতীর্থ (১৯৭৭), চারজন (২০০৪, সম্পাদক: ভূমেন্দ্র গুহ ও ফয়সাল শাহরিয়ার)।
জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভারতবর্ষের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অন্তর্গত বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত আর মাতা কুসুমকুমারী দাশ। তার পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ) পরগণার কুমারভোগ নামক স্থানে ‘গাওপাড়া’ গ্রামের নিবাসী ছিলেন। যা পদ্মায় বর্তমানে বিলীন হয়ে গেছে। স্থানটি মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় অবস্থিত।
জীবনানন্দের মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন গৃহিণী, কিন্তু তিনি কবিতা লিখতেন। তার সুপরিচিত কবিতা আদর্শ ছেলে (আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড়ো হবে) আজও শিশুশ্রেণির পাঠ্য। জীবনানন্দ ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান; তার ডাকনাম ছিল মিলু।
১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে আট বছরের জীবনানন্দকে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হন। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন তার বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচনার সূচনা হয়। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (বর্তমানে মাধ্যমিক বা এসএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দু'বছর পর ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (এইচএসসি) পাশ করেন। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার উদ্দেশ্যে বরিশাল ত্যাগ করেন।
১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ওই বছরেই ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় তার প্রথম কবিতা ছাপা হয়। কবিতার নাম ছিল ‘বর্ষ আবাহন’।
১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি আইন বিষয়ে পড়া শুরু করলেও অল্পতেই ছেড়ে দেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জীবনানন্দ কলকাতার সিটি কলেজে শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন।
অধ্যাপনা করেছেন বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যার মধ্যে আছে সিটি কলেজ, কলকাতা (১৯২২-১৯২৮), বাগেরহাট কলেজ, খুলনা (১৯২৯); রামযশ কলেজ, দিল্লী (১৯৩০-১৯৩১), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৯৩৫-১৯৪৮), খড়গপুর কলেজ (১৯৫১-১৯৫২), বড়িশা কলেজ (অধুনা 'বিবেকানন্দ কলেজ', কলকাতা) (১৯৫৩) এবং হাওড়া গার্লস কলেজ, কলকাতা (১৯৫৩-১৯৫৪) তার কর্মজীবন আদৌ মসৃণ ছিল না। চাকরি তথা সুস্থির জীবিকার অভাব তাকে আমৃত্যু কষ্ট দিয়েছে।
একটি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। স্ত্রী লাবণ্য দাশ স্কুলে শিক্ষকতা করে জীবিকার অভাব কিছুটা পুষিয়েছেন। তিনি আমৃত্যু হাওড়া গার্লস কলেজে কর্মরত ছিলেন। দুই দফা দীর্ঘ বেকার জীবনে তিনি ইন্সুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন এবং প্রধানত গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালিয়েছেন। এ ছাড়া ব্যবসার চেষ্টাও করেছিলেন বছরখানেক। দারিদ্র্য ও অনটন ছিল তার কর্মজীবনের ছায়াসঙ্গী।
অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী জীবনানন্দ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর কলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হন। ট্রামের ক্যাচারে আটকে তার শরীর দলিত হয়ে গিয়েছিল। ভেঙ্গে গিয়েছিল কণ্ঠা, ঊরু ও পাঁজরের হাড়। গুরুতরভাবে আহত কবিকে নেওয়া হয় শম্ভূনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। এখানেই তিনি চিকিৎসক ও সেবিকাদের সব প্রচেষ্টা বিফল করে দিয়ে ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
আরএইচ/
খবরটি শেয়ার করুন